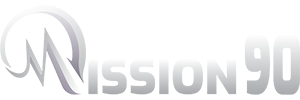ফটোশপের এই যুগে ছবি এডিট করা খুবই সহজ কাজ। অনেকেই নিছক মজা করার উদ্দেশ্যে, কিংবা সোশ্যাল মিডিয়া বেশি লাইক বা শেয়ার পাওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ছবি এডিট করে ছড়িয়ে দেয়। এরকম কিছু এডিট করা ছবি মাঝে মাঝে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, মূল ছবিটির পরিবর্তে এডিট করা ছবিটিকেই সবাই সত্যি ভেবে বিশ্বাস করতে থাকে এবং শেয়ার করতে থাকে। চলুন দেখে নেওয়া যাক বিশ্বের সবচেয়ে বেশি শেয়ার হওয়া কিছু ছবি, যেগুলো আসলে এডিট করা, কিন্তু মানুষ বিপুল সংখ্যক মানুষ সেগুলোকে সত্যি মনে করে।
চীনের ১০০ কিলোমিটার লম্বা যানজট

বিশ্বের সবেচয়ে বেশি জনসংখ্যার দেশ চীনে যে যানজট হবে, তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে! ২০১০ সালের আগস্টের ১৪ তারিখে চীনে সত্যি সত্যিই বিশ্বের ইতিহাসের দীর্ঘতম যানজট সৃষ্টি হয়েছিল। যানজটটি তৈরি হয়েছিল চীনের ন্যাশনাল হাইওয়ে ১১০ এবং বেইজিং-তিব্বত এক্সপ্রেসওয়ে জুড়ে। এটি প্রায় ১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা জুড়ে যানবাহনের চলাচল থামিয়ে দিয়েছিল এবং অন্তত ১২ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।


কিন্তু যে ছবিটি ইন্টারনেটে হাইওয়ে ১১০ এর যানজটের নাম দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে, সেটি মোটেও চীনের ঐ যানজটের ছবি না। ছবিটি ফটোশপে এডিট করা। ছবিটিতে যে ফটোশপের মাধ্যমে অতিরিক্ত গাড়ি বসানো হয়েছে, শুধু তাই নয়, এখানে রাস্তার লেনগুলোকেও প্রশস্ত করা হয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা, এটি আদতে চীনের কোনো রাস্তাই না। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের লস অ্যাঞ্জেলসের I-405 ফ্রিওয়ে।
পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ পরিদর্শকালে আইনস্টাইন

২০১১ সালে প্রথম এই ছবিটি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ে। এই ছবি অনুযায়ী, ১৯৬২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেভাদা অঙ্গরাজ্যের মরুভূমিতে সামরিক বাহিনী যখন পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষা চালাচ্ছিল, তখন তা পরিদর্শন শেষে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন তার সাইকেলে চড়ে সেখান থেকে ফিরে আসছিলেন। এই দাবিটি অবাস্তব এই কারণে যে, আইনস্টাইন মৃত্যুবরণ করেছিলেন ১৯৫৫ সালে, এই ঘটনার ছয় বছরেরও আগে।
এই ছবিটি মূলত দুটি ছবিকে একত্রিত করে তৈরি করা হয়েছে। ছবির সামনের অংশটুকু, অর্থাৎ আইনস্টাইনের সাইকেল চালানোর অংশটুকু নেওয়া হয়েছে ১৯৩৩ সালে সান্তা বারবারায় তোলা তার একটি ছবি থেকে। আর পেছনের অংশটুকু সত্যি সত্যিই ১৯৬২ সালের পারমাণবিক বিস্ফোরণের ছবি। ছবিতে আইনস্টাইনের সাইকেলের সাথে ছায়ার দৈর্ঘ্যের অনুপাত এবং অন্যান্য দর্শকদের সাথে তাদের ছায়ার দৈর্ঘ্যের অনুপাতের পার্থক্য লক্ষ্য করলেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ছবিটি ফটোশপের মাধ্যমে তৈরি।


ছবিটি ইন্টারনেটে প্রথমে প্রচার করা হয়েছিল মূলত মজা করার উদ্দেশ্যে, কিন্তু অনেক ওয়েবসাইট একে সত্য ভেবে প্রচার করতে থাকে। অনেকে আবার এর সাথে আইনস্টাইনের বিভিন্ন উক্তিও জুড়ে দেয়, যে উক্তিগুলোও অধিকাংশই ভুয়া। যেমন, কিছু কিছু সাইটে লেখা হয়, আইনস্টাইন বলেছেন,
আবার অন্য কিছু সাইটে লেখা হয়, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের কলাকুশলীদের বিপদসংকুল জীবন

ন্যাশনাল এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ছবি। ন্যাশনাল জিওফিগ্রাফিকের ক্যামেরাম্যান এবং পরিচালকরা কত ঝুঁকি নিয়ে ডকুমেন্টারি নির্মাণ করেন, তার উদাহরণ হিসেবে এই ছবিটি প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। বাস্তবে বন্যপ্রাণীদের উপর চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাজ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হলেও এই ছবিটি সম্পূর্ণ বানোয়াট। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক তো না-ই, এটি ভালুকের তাড়া খেয়ে দৌড়ানোর ছবিও না। এটি শুধুই মজা করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে তোলা ছবি।
ছবিতে নীল জামা পরা দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকটির নাম টিম স্পার্কস। তিনি একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা। ২০১১ সালে তিনি এবং তার দল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো অঙ্গরাজ্যের বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন নতুন একটি চলচ্চিত্রের লোকেশন বাছাইয়ের জন্য।


ভালুক
কয়েকদিন ঘোরাঘুরির পরেও পছন্দ অনুযায়ী লোকেশন না পেয়ে যখন তারা বিরক্ত, তখনই তিনি এবং তার সহকর্মীরা তাদের পরিবারদেরকে চমকে দেওয়ার জন্য মজা করে এই ছবিটি তোলেন। বলাই বাহুল্য, মূল ছবিটিতে কোনো ভালুক ছিল না, সেটি পরবর্তীতে সম্পাদনা করে যোগ করা হয়।
এমজিএমের বিখ্যাত সিংহের লোগোর শ্যুটিং


হলিউডের বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এমজিএমের (মেট্রো গোল্ডউইন মায়ার) লোগো হচ্ছে একটি সিংহের মুখ। শুধু স্থির লোগো না, তাদের প্রতিটি চলচ্চিত্র শুরু হওয়ার পূর্বে সিংহের গর্জনের একটি ভিডিও দেখানো হয়। ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া একটি ছবির মাধ্যমে দাবি করা হয়, এমজিএম একটি সিংহের চারটি পা বেঁধে এরপর তাকে দিয়ে গর্জন করিয়ে ঐ দৃশ্যটি ধারণ করেছিল।
ছবিটি ইন্টারনেটে প্রচন্ড জনপ্রিয়তা পায়। অনেকেই একে সত্যি ভেবে শেয়ার দেয়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, ছবিটি ফটোশপ করা।মূল ছবিটি ধারণ করা হয় ২০০৫ সালে, যখন ইসরাইলের একটি চিড়িয়াখানায় স্যামসন নামে দুই বছর বয়সী একটি সিংহ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে হাসপাতালে নিয়ে ক্যাটস্ক্যান করানো হয়। সেই ছবিটিই পরে কেউ সম্পাদনা করে, সাদা রংয়ের ক্যাটস্ক্যান মেশিনের উপর এমজিএমের নাম বসিয়ে ইন্টারনেটে ছেড়ে দেয়।

এমজিএমের ওয়েবসাইটে অবশ্য অনেক আগে থেকেই তাদের লোগো নির্মাণের সচিত্র ইতিহাস দেওয়া আছে। লোগো তৈরির জন্য তাদের কোনো সিংহকে বাঁধার প্রয়োজন হয়নি, বরং ট্রেনিং প্রাপ্ত সিংহকে সরাসরি ক্যামেরার সামনে দাঁড় করিয়েই তারা চিত্রধারণ করেছিল।
আয়ারল্যান্ডের ক্যাসেল আইল্যান্ড

বেশ রহস্যময় একটি দ্বীপ-দুর্গ এটি। সমুদ্রের বুকে খাড়া হয়ে উঠে যাওয়া দ্বীপের উপর ভূতুড়ে এ দুর্গের অবস্থান। ইন্টারনেটে শত শত সাইটে বিশ্বের রহস্যময় বা আকর্ষণীয় স্থানের তালিকায় স্থান পেয়েছে এই ছবিটি। দাবি করা হয়, এটি আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে অবস্থিত একটি দুর্গ, যার নাম ক্যাসেল আইল্যান্ড। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এটি মূলত দুইটি ভিন্ন ছবিকে সুনিপুণভাবে জুড়ে দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।
ছবির মূল দ্বীপটির অবস্থান থাইল্যান্ডে। এর নাম খাও ফিং কান আইল্যান্ড, যা জেমস বন্ড আইল্যান্ড নামেই বেশি পরিচিত। অন্যদিকে দুর্গটি জার্মানীর লিচেনস্টাইন দুর্গের চূড়ার অংশবিশেষ। এই দুটো ভিন্ন ছবিকেই ফটোশপের সাহায্যে সম্পাদনা করে তৈরি করা হয়েছে অস্তিত্বহীন ক্যাসেল আইল্যান্ড, যা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে ধোঁকা দিতে সক্ষম হয়েছে।


প্রেসিডেন্ট বুশের উল্টো বই ধরা সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডাব্লিউ বুশের বোকামির উদাহরণ দিতে গিয়ে প্রায়ই এই ছবিটি ব্যবহার করা হয়। এখানে দেখা যায়, বুশ একটি বই পড়ার ভান করছেন, কিন্তু তিনি উল্টো করে ধরে রেখেছেন। বাস্তবে এই ছবিটিও এডিট করা।
ছবিটির দিকে ভালোভাবে লক্ষ্য করলেই ব্যাপারটা বোঝা যায়। মেয়েটির হাতের বইটির পেছনের কভারের দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রচ্ছদের একেবারে ডান পাশে ছবিটির পরেও প্রায় দুই ইঞ্চির মতো জায়গা ফাঁকা আছে। কিন্তু বুশের হাতে থাকা বইয়ের প্রচ্ছদের ছবিটির শেষে খুবই কম ফাঁকা জায়গা। তাছাড়া ছবিটি পুরোপুরি সোজা না, কিছুটা বাঁকা।

সবচেয়ে বড় কথা, মেয়েটির হাতে থাকা বই অনুযায়ী পেছনের কভারের ছবিটির মধ্যে লাল রং আছে বাম পাশে, আর কালো রং ডান পাশে। বুশ যদি বইটি উল্টে ধরতেন, সেক্ষেত্রে এই রং দুটো বিপরীত পাশে চলে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটি হয়নি। অর্থাৎ যে ছবিটি ফটোশপে এডিট করেছে, সে শুধু ছবিটিকে উপর-নিচে পাল্টে দিয়েছে, কিন্তু আড়াআড়ি বরাবর পাল্টাতে ভুলে গিয়েছিল।

হাঙ্গরের
এই ছবিটি ২০০১ সালে বেশ জনপ্রিয় ছিল। তখন ইমেইলের মাধ্যমে এই ছবিটি পাঠিয়ে বলা হতো, দেখতে হলিউড চলচ্চিত্রের দৃশ্যে মতো মনে হলেও এটি আসলে দক্ষিণ আফ্রিকার সমুদ্র তীরে অনুশীলনরত এক ব্রিটিশ নৌসেনার উপর সত্যিকার হঙ্গরের আক্রমণ। এবং ছবিটি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক কর্তৃক বর্ষসেরা ছবি নির্বাচিত হয়েছে।
বাস্তবে ছবিটি দুটি ভিন্ন ছবির সমন্বয়ে তৈরি। ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টারটির ছবি নেওয়া হয়েছে মার্কিন বিমান বাহিনীর তোলা একটি ছবি থেকে। হেলিকপ্টারটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকো উপসাগরে অবস্থিত গোল্ডেন গেট ব্রিজের সামনে অনুশীলনরত ছিল। এডিট করা ছবিটির পেছনেও গোল্ডেন গেট ব্রিজের অংশবিশেষ দৃশ্যমান। অন্যদিকে হাঙ্গর মাছের ছবিটি নেওয়া হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার এক ফটোগ্রাফারের তোলা ছবি থেকে।
বাস্তবে দক্ষিণ আফ্রিকার সমুদ্রতীরে গোল্ডেন গেটের মতো দেখতে কোনো ব্রিজ নেই, বা সান ফ্রান্সিসকো উপসাগরে এরকম হাঙ্গর মাছও নেই। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক বিবৃতি দিয়ে এই ছবির সাথে তাদের সম্পৃক্ততা অস্বীকার করেছিল।
মহাত্মা গান্ধীর নৃত্য

এই ছবিটিও ইন্টারনেটে বেশ প্রচলিত। এখানে দেখা যায়, মহাত্মা গান্ধী কোনো অনুষ্ঠানে এক শেতাঙ্গিনীর সাথে নাচছেন। অনেকের মতে, এই ছবিটির কোনো ভিত্তি নেই। ছবিটি এডিট করা হয়নি, তবে যিনি নেচেছেন, তিনি মহাত্মা গান্ধী না। তিনি একজন অভিনেতা, যিনি গান্ধীর মতো করে সেজেছেন।
ওপিন্ডিয়া নামে এই ওয়েবাইটে দাবি করা হয়, এই ছবিতে নৃত্যরত ভদ্রলোকের পেশীবহুল হাত এবং পায়ের জুতো সত্যিকার গান্ধীর সাথে মিলে না। অন্যদিকে কিউরিয়াস পয়েন্ট নামে এই ওয়েবসাইটে ছবিটির ক্যাপশন পোস্ট করে দাবি করা হয়, ছবিটি অস্ট্রেলিয়ার সিডনীর একটি পার্টিতে তোলা, যেখানে একজন অভিনেতা গান্ধীকে অনুকরণ করছিলেন।